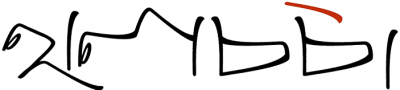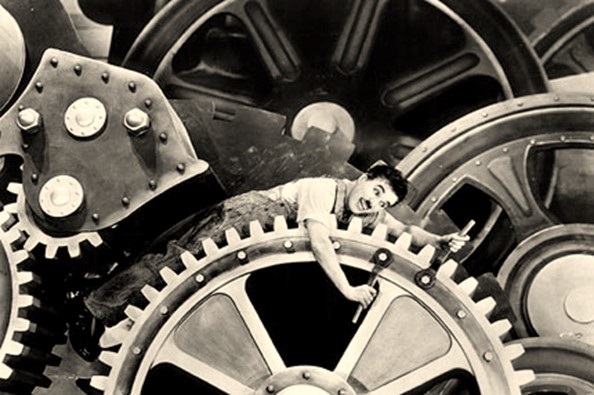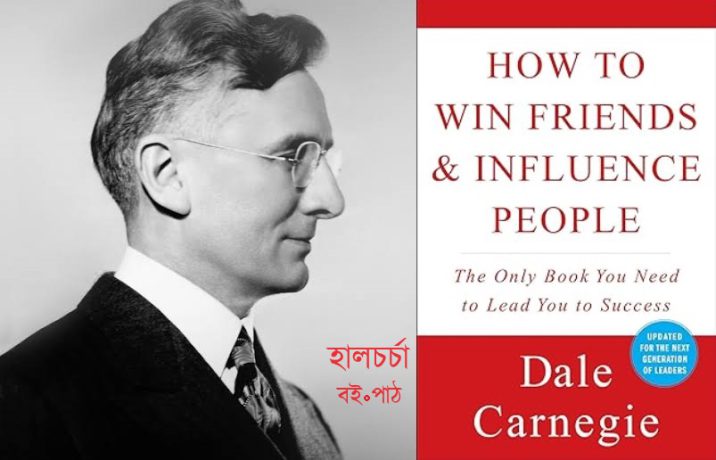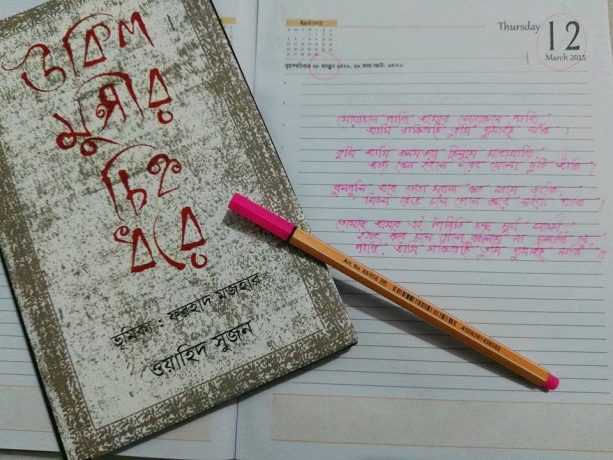সাখাওয়াত হোসেন
আমার কেন জানি মনে হয়, হুমায়ূন আহমেদের সবচেয়ে ভুল বোঝা চরিত্রটা হলো হিমু। হিমু আমরা বুঝিনি। হিমু আমরা ধরতে পারিনি। হিমু আমরা দেখতে পারিনি এবং সবচেয়ে দুঃখনজনক সত্য হলো, হিমুর একটা টুকরোও আমরা পড়তে পারিনি।
হুমায়ূন ‘হিমু’কে নিয়েছিলেন সুবোধ ঘোষের ‘শুন বরনারী’ থেকে। যদিও বেশ তফাৎ আছে দুই হিমুর মধ্যে। হুমায়ূন একটা চরিত্র নিয়েছেন। যে পথে-ঘাটে হাঁটবে খালি পায়ে। হলুদ পাঞ্জাবি পরবে। নির্দিষ্ট কোনো ঘর থাকবে না। পরিবার থাকবে না। কোনো গন্তব্যও থাকবে না। আমরা এই চরিত্রটাই পড়েছি। সে অদ্ভুত সব কথা বলে। মজার মজার কাণ্ড করে। হিমু এবং হার্ভার্ড পিএইচডি বল্টুভাই উপন্যাসে হিমু পরিমল নামে একজনের হাত মাজারের রেলিং-এ আটকে ফেলেছিল তাকে কোনোরকম স্পর্শ করা ছাড়াই, শুধু কথা বলে। ওটা অলৌকিক নয়। ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু অলৌকিক হিমুর সাথে হয় না— তা বলা যাবে না। আমরা সেটা পড়ি। মজা পাই। আমরা যেটা পড়ি না, কেন হিমু হাঁটে? কেন মাথার উপর রোদ নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এক যুবক বিড়বিড় করে যায় একা? সে আদৌ মায়া কাটাতে পেরেছে জগত-সংসারের? তার চোখে কি জল জমে কখনও? সেও কি কান্না করে?
হিমু হালকা একটা চরিত্র হতো, যদি না তার কুৎসিত একটা শৈশব থাকতো। হিমুকে ডার্ক মানতেই রাজি নন পাঠক সমাজ। অথচ প্রায় প্রতিটা বইয়েই হিমুর ছোট্ট ছোট্ট ভয়ংকর শৈশব তুলে এনেছিলেন হুমায়ূন শুধুমাত্র এইটুকুন ধারণা দেওয়ার জন্য যে, উদোম পায়ে পথে-ঘাটে শুধু হাঁটাই হিমু নয়। হিমু আরও গভীর কিছু। এবং প্রায় প্রতিটা বইয়েই পাঠক সেটা পড়ার বাইরে রেখেছেন। ফলে হিমু হয়ে দাঁড়িয়েছে নিছক মজার কোনো চরিত্র, অনর্থক বিনোদনের খুচরো মাধ্যম, আপাদমস্তক হলুদ নিয়েও রঙহীন কোনো মানুষ।
হিমুর বাবা সুস্থ ছিলেন না। ছিলেন মানসিকভাবে অসুস্থ একজন মানুষ। যিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, পড়াশোনা করে যদি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায়, ট্রেনিং দিয়ে মহাপুরুষ হওয়াও সম্ভব। হিমু ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো, প্রধান এবং একমাত্র এক্সপেরিমেন্ট। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, গিনিপিগ। যদিও বেশীদিন পাননি, তবে যেটুকুন সময় পেয়েছেন হিমুকে তৈয়ার করেছেন। গুঁজে দিয়েছেন ভয়ানক শৈশব। হিমুর শৈশব সম্পর্কিত অল্পকিছু ঘটনা দিয়ে এর ভয়াবহতা অনুভব করা সম্ভব।
১. খুব ছোটবেলায় হিমুকে একটা টিয়ে পাখি কিনে দিয়েছিলেন তার বাবা। হিমু পাখি পেয়ে খুব খুশি। রাতদিন পাখির সঙ্গে থাকলো। আদর করল। ভালোবাসলো। পাখিটাকে কথা বলা শেখালো। যেদিন কথা বলল, সেদিন বাবা পাখিটাকে গলা টিপে মেরে ফেললেন। এটা ছাড়াও বিভিন্ন খেলনা কিনে দিতেন তিনি হিমুকে। খেলা শুরু করার পর ভেঙে ফেলতেন। শুধুমাত্র এটা বোঝানোর জন্য, মায়া জিনিসটা তাকে ত্যাগ করতে হবে। মায়ার কোনো একক সত্ত্বা নেই। ওটা সামগ্রিক। তুমি জগতের সব পাখি ভালোবাসবে। নির্দিষ্ট কোনো পাখি নয় শুধু। তুমি জগতের সব মানুষ ভালোবাসবে, নির্দিষ্ট কোনো মানুষকে নয়।
২. হিমু মাকে জন্মের পর থেকে পায়নি। মায়ের চেহারাটাও দেখেনি। মৃত্যুর পর মায়ের সমস্ত ছবি নষ্ট করে ফেলেছেন বাবা। সব ছবি নয়। একটা ছবি রেখেছেন। আট ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চি সাইজের এই ছবিটা বাবা তার বিছানার তোষকের নিচে খামের ভেতর সিলগালা করে রেখেছেন। সঙ্গে মায়ের লেখা একটা ডায়েরিও। এই খাম খোলার শর্ত আছে। যেদিন হিমুর হৃদয় সত্যিকার অর্থে আনন্দে পরিপূর্ণ হবে, শুধুমাত্র সেদিনই সে খামটা খুলতে পারবে। শর্ত শেষ নয়। খামটা খোলার পর ছবিটা একবার দেখে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ছবি, ডায়েরি, খাম সব। বাবা জানেন, একজীবনে বহুবার সত্যিকার আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হওয়ার পরও হিমু ‘আর কোনোদিন দেখতে না পারার ভয়ে’ এই ছবি কোনোদিনই দেখবে না। জন্ম থেকে মা হারা একজন যুবকের জন্য বিষয়টা কি পরিমাণ নির্মম ভাবা যায়?
‘হিমু’ -এর শেষাংশ পড়ার পর আমার কেন জানি মনে হয়, হিমুর মায়ের মৃত্যু হিমুর জন্মের সাথে সাথে হয়নি। কিছু দিন কিংবা কিছু মাস পর হয়েছে। ‘হিমু’ উপন্যাসের শেষদিকে হিমু চেতন আর অবচেতন জগতের মাঝখানে পৌঁছায় কুকুরের কামড় খেয়ে। তখন বাবার সাথে তার একটা কথোপকথন হয়। কাল্পনিক কথোপকথন। ঐ কথোপকথনে বাবা তাকে ‘হিমু’ ডাকে না। ডাকে, খোকা। হিমু জিজ্ঞেস করার পর বাবা উত্তর দেয়, ‘তোর মা তোকে খোকা ডাকতো।’ এই কথোপকথন কিন্তু বাস্তবিক নয়। পুরোটাই হিমুর অবচেতন মনের তৈয়ার করা দৃশ্য, সংলাপ।
অর্থাৎ, হিমুর মা হিমুকে খোকা ডাকতো, বিষয়টা বাবা তাকে জানাচ্ছে এমন নয়, বিষয়টা হিমুর অবচেতন মন জানে। ছোটবেলার অধিকাংশ স্মৃতিই বড়ো হওয়ার পর গায়েব হয় মাথা থেকে। মায়ের গায়ের রঙ শ্যামলা, একটা চোখ অপর চোখ থেকে অল্প একটু বড়ো, কাজল পরতো, অসম্ভব সুন্দর ছিল, মায়ের মুখ নিঃসৃত ঐ খোকা ডাক- এইসব কিভাবে থাকলো হিমুর মাথায়, তা অবশ্য অস্পষ্ট।
৩. বাবার মৃত্যুর পর হিমু বাবার দিককার কোনো আত্মীয়-স্বজনদের পায়নি। তাকে যেতে হয়েছে মায়ের দিককার আত্মীয়-স্বজনদের নিকট। যাওয়ার এই বিষয়টা নিশ্চিত করেছেন খোদ হিমুর বাবা-ই। তিনি চেয়েছেন পুত্রের শৈশব মামাদের সঙ্গে কাটুক। কারণ হিমুর মামারা পিশাচশ্রেণীর মানুষ। মন্দের সাথে না থাকলে ভালো ঠিক কতটা ভালো, জানা হবে না। মামারা সত্যিই পিশাচ ছিলেন। গর্ভবতী বিড়াল জবাই, কোঁচ গেঁথে হওয়া মৃত্যুর আগে গ্রামের নির্দোষ চারজনকে ডেথ কনফশনে ফাঁসিয়ে দেওয়া সহ ভয়ানক কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে বইতে। মন্দ মানুষদের সাথেও অতিদ্রুত হিমুর সম্পর্ক সহজ হওয়ার পেছনে শৈশবের মামাবাড়ি অনেকটাই প্রভাব রাখে- তা আর বলতে।
৪. সর্বশেষ যেটি, সেটি যেকোনো মানুষকেই মানসিকভাবে চরম ধাক্কা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। বিশেষ করে ঐ বয়সে। হিমু খুব দ্রুত টের পেয়েছিল, তার মায়ের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। তার মাকে মেরে ফেলা হয়েছে। এবং কাজটা করেছেন তার বাবা। কারণ, পুত্রের মহাপুরুষ হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড়ো বাধা হবেন মা। বিষয়টা সরাসরি স্বীকার না করলেও সূক্ষ্ণভাবে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বাবা, ‘তোর মা কিভাবে মারা গিয়েছিল তোকে খুঁজে বের করতে হবে। তোকে জ্ঞানী হতে হবে। আমি যা করেছি, তোর জন্য করেছি।’
মৃত্যুর আগে হিমুর বাবা স্বপ্নে দেখেন স্ত্রীকে। এই বিষয়টা ইন্টারেস্টিং। কারণ, এই জায়গায় হিমুর বাবাকে প্রথমবার কিছুটা বোধহয় উপলব্ধি করতে দেখা যায়, মা হারিয়ে চলা দীর্ঘ পথটা বড্ড কষ্টের হবে পুত্রের জন্য। পুত্রের এই কষ্টের জন্য তিনি দায়ী। আক্ষেপটা ফুটে উঠে স্বপ্নের ভেতর। মা স্বপ্নে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করেন, ‘ওর কি কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে? কোনো মেয়ে ভালোবেসে তার হাত ধরেছে?’ বাবা উত্তর দেন, ‘না। সে মহাপুরুষ হওয়ার সাধনা করছে। তার জন্য নারীসঙ্গ নিষিদ্ধ।’ মা চোখ মুছে রাগী স্বরে বলেন, ‘সে সাধনা করছে না, কচু করছে। তাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে আসো। আমি থাবড়ায়ে তার মহাপুরুষগিরি ছুটায়ে দেবো।’ এই আক্ষেপ বলি কিংবা অপরাধবোধ হিমুর বাবার অবচেতন মনে ছিল। সচেতন মনে কোনোদিন স্বীকার করেননি। কোথাও না কোথাও পুড়েছেন ঠিক, অন্য একটা জীবন পুত্রের হলেও হতে পারতো।
হিমুর প্রথম উপন্যাসের নাম হিমু নয়। ময়ূরাক্ষী। এটা একটা নদী। ক্লাস সিক্সে পড়াকালীন এই নদীর নাম প্রথম মাথায় আসে হিমুর। যদিও সে তখনও জানে না, এই নামে কোনো নদী আছে কিনা। একটা স্যার তখন বলেছিলেন তাকে, না থাকলে নাই। এটা তোর নদী। হিমু এই নদীকে স্বপ্ন দেখে প্রথমবার, এই ঘটনার তিন বৎসর পর। নদীর বর্ণনাটা এইরকম। ছোট্ট একটা নদী। নদীর জল স্বচ্ছ। নিচে বালি পর্যন্ত স্পষ্ট। দু’পাড়ের ঘাস সবুজ। ওপাড়ে একটা পাকুড় গাছ। বিশাল। সেই গাছে বিষন্ন গলায় একটা ঘুঘু ডাকে। সেই ডাকে কান্না মিশে আছে। নদীর ধার ধরে পানি ছিটাতে ছিটাতে সবুজ ডোরাকাটা শাড়ি পরা একটা মেয়ে হেঁটে যায়।
আপাদমস্তক হিমু পড়ার পরও খুব কম মানুষের পক্ষেই ধরতে পারা কঠিন, ময়ূরাক্ষী আদৌ কোনো নদী নয়। এটা হচ্ছে হিমুর ঐ সংসার, ঐ পথ, ঐ গন্তব্য, ঐ ঘর, ঐ জীবন যেটা বাস্তবে সে কখনই যাপন করতে পারেনি, পারছে না এবং পারবেও না। কারণ, ওখানে শুধু নদী নেই। আছে একটা বিশাল পাকুড় গাছও, যে গাছে ঘুঘু ডাকে বিষণ্ণ স্বরে। এই ডাক হিমুরই গোপন দুঃখ। এই ডাকে তার চোখ ভিজে আসে। ঐ নদী জলে সে বেশিক্ষণ পা ডুবিয়ে বসেও থাকতে পারবে না, কারণ পাড় ধরে সবুজ ডোরাকাটা শাড়ি পরা একটা মেয়ে হেঁটে যায়। এই নারী তার অচেনা, তার মুখ স্পষ্ট নয়, অথচ একইসঙ্গে এই নারী তার বহুদিনের চেনা। জন্ম জন্মান্তরের পরিচয়।
ময়ূরাক্ষী উপন্যাসের একদম শেষদিকে এই নারীর পরিচয় দেওয়া হয়। এই নারী হিমুর মা, যাকে হিমুর বাবা হত্যা করেছেন। অর্থাৎ, হিমুর কাল্পনিক ময়ূরাক্ষী বিষাদ আর মৃত্যুতে আচ্ছন্ন। চোখ খুললে হিমুকে নিজের সহ জগতের সমস্ত ঘটনা, বিষয়বস্তু ও মনুষ্য নিয়ে নির্মোহ থাকতে হয়, পাথর থাকতে হয়, স্থির থাকতে হয়। এটা বাবার তৈয়ার করা জগত। বিপরীতে ময়ূরাক্ষী তার নিজের তৈয়ার করা ঐ জগত, যেটা বাবা সহ পারিপার্শ্বিক সবার থেকে খুব যত্ন করে লুকানো। যেখানে সে চোখ ভিজাতে পারে অনায়াসে, যেখানে সে আটকাতে পারে মায়ায়। মূলত হিমুর দুই জগতই বাসযোগ্য নয়। সে না পারবে রিয়েলিটিতে বাস করতে, না পারবে ইমাজিনেশনে। দু’টোতেই প্রগাঢ় শূন্যতা, ভয়াবহ বিষাদ, শুকনো পথ, স্যাঁতসেঁতে নদীর পাড়।
হিমুর বাবা সফল হয়েছিলেন নাকি সফল হননি, তা স্পষ্ট নয়। হিমুর মতোই অস্পষ্ট। ‘এবং হিমু…’ উপন্যাসে আইসিইউতে বদরুল সাহেবকে রেখে যখন বের হয়ে পড়ে হিমু, আর ইরা বলে, ‘আপনার বন্ধুর পাশে থাকবেন না?’ হিমু ছোট্ট করে উত্তর দেয়, ‘না।’ ইরা অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞেস করে, ‘আপনাকে যদি বলি আমার হাত ধরতে, আপনি কি রাগ করবেন?’ হিমু জবাব দেয়, ‘আমি রাগ করবো না। কিন্তু ইরা, আমি তোমার হাত ধরবো না। হিমুরা কখনো কারও হাত ধরে না।’
হিমু ডুব দিতে পারে খুবই শান্ত থেকে। কোনোরকম উচ্ছ্বাস ছাড়াই ফেরত আসতে পারে আবার। মায়া ছেড়ে আসায় ওর জুড়ি মেলা ভার। হিমু পড়তে পড়তে আমার কখনো সখনো মনে হয়, হিমুর বাবা সফল। আবার ‘আজ হিমুর বিয়ে’ উপন্যাসে যখন খালা কাঁচা হলুদ বেঁটে হিমুর গায়ে মাখিয়ে ধমক দিতে দিতে গোসল করিয়ে দেন, হিমুর চোখে জল জমে। খালা অবাক হন। আমি অবাক হই। ওদের কথোপকথন।
‘কিরে কাঁদছিস কেন? চোখে পানি কেন?’
‘মহাপুরুষ ট্রেনিং-এ ফেইল করেছি বলে চোখে অশ্রু।’
‘হেঁয়ালি করে কথা বলবি না। কী সমস্যা বল।’
‘তোমার আদরটাই সমস্যা। এত আদর এত মমতা নিয়ে কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি।’
এইটুকুন পড়ে মনে হয়, হিমুর বাবা পুরোপুরি সফল হননি বোধহয়। ‘হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম’ উপন্যাসে এই মতের পক্ষে ও বিপক্ষে ভয়ানক নির্দয় একখানা দৃশ্য বিদ্যমান। যারা হিমু খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন, তারা ঠিক ধরে নিতে পারবেন, হিমুর সর্বমোট একুশটা উপন্যাসের ভেতর যে নারী সবচেয়ে বেশী টেনে ধরেছিল হিমুর পথ, আগলে দাঁড়িয়েছিল কিংবা বলা যায় গন্তব্যহীন একটা যাত্রার প্রতি চরম আক্ষেপে চোখে জল এনে দিয়েছিল, সে রুপা নয়। মারিয়া।
যারা হিমু সিরিজের মাত্র দু’টো উপন্যাস পড়তে চান, আমি তাদেরকে ময়ূরাক্ষীর পর ‘হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম’পড়তে সাজেস্ট করি সবসময়। এই উপন্যাসের শেষদিকে হিমু মারিয়া থেকে বিদায় নেয়। মারিয়া দাঁড়িয়ে থাকে। পরবর্তী অংশ হিমুর বয়ানে, ‘কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার ভেতর একধরণের বিভ্রম তৈরী হলো। মনে হলো আমার আর হাঁটার প্রয়োজন নেই। মহাপুরুষ না, সাধারণ মানুষ হয়ে মমতাময়ী এই তরুণীটির পাশে এসে বসি। যে নীলপদ্ম হাতে নিয়ে জীবন শুরু করেছিলাম, সে পদ্মগুলি তার হাতে তুলে দিই।’
হিমু কখনই পারিপার্শ্বিক ঘটনা, পরিস্থিতি, মনুষ্য ও বন্ধন নিয়ে পুরোপুরি নির্মোহ হতে পারেনি আবার হিমু কখনই গাঢ় আবেগ মাখা কোনো বন্ধনে পুরোপুরি জড়াতেও পারেনি। বরং বসবাস করেছে মধ্যবর্তী একটা জায়গায়। এই জায়গায় সে গন্তব্যহীন হাঁটা হাঁটে, এই জায়গায় হাঁটতে হাঁটতে তার ক্লান্তিও জাগে, সে তখন বসে পড়ে চুপচাপ। ময়ূরাক্ষী বের করে আনে কল্পনায়। ঠাণ্ডা জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকে। চোখ ভেজায়।
এই জায়গায় দাঁড়িয়ে হিমু একটা ঠেলাগাড়িওয়ালাকে জীবন বাঁচানোর বদলে উল্টো থাপ্পড় দেয়। এই জায়গায় বসে মাথায় হাত বুলায় পথশিশুর। কোনো একটা শিশুর ইচ্ছাপূরণে হাতির বাচ্চা ভাড়া করে ফেলে। মন্দ একটা মানুষকে খুব সহজে বদলে দেয়। বৃষ্টিতে ভিজিয়ে নির্মল করার ক্ষমতা রাখে কড়া পাপ। বিভ্রম সৃষ্টি করে যায় অনর্গল। এই মধ্যবর্তী জায়গায় বসবাস বলেই হিমু জটিল। চূড়ান্ত জটিল। হিমু কোনোদিনও ক্লাস নাইন-টেন পড়ুয়া কিশোর-কিশোরীর পাঠ্য নয়, ছিলও না। হুমায়ূন পড়া শুরু করার মাধ্যম তো নয়ই। সহজ ভঙ্গিতে লেখা বলে হিমু পড়া সহজ। ধরা সহজ নয়।
আমাদের প্রজন্ম হিমুর হাঁটা গলাধঃকরণ করে, আলাপের অংশ রাখে হলুদ রঙ, হিমুর প্রতি রুপার প্রবল প্রেম, ছাদের কার্নিশ, ইনট্যুইশন, রসিকতা। ওরা যেটি রাখে না, সেটি হলো একটা নদী। ময়ূরাক্ষী। যেটি বাস্তবে হিমুর কখনই হয়নি। হওয়ার উপায় ছিল। মানুষ ছিল। পথ ছিল। কিন্তু হয়নি কারণ ঐ নদীর পাড় ধরে সবুজ ডোরাকাটা শাড়ি পরে যে দুঃখী নারী হেঁটে যায়, ঐ নারীকে কখনই দেখা হয়নি তার, কোনোদিন যার মায়ামাখা হাত বিলি কাটেনি চুলে, কখনই যে ঠোঁটজোড়া স্পর্শ করেনি ক্লান্ত ললাট। ফলে পৃথিবীর সব নারীর মুখচ্ছবিতে ঐ নারী ফুটে ওঠে। পৃথিবীর সব নারীর হাত হয়ে উঠে ঐ নারীর হাত। সব চুম্বন শুধুই ঐ নারীর চুম্বন। হিমুকে তাই সব ছেড়েছুড়ে হাঁটতে হয়। না হাঁটলেও সে পারতো। কিন্তু তাতে বৃথা যাবে একটা মৃত্যু। ঐ মৃত্যুর দায়ভার হিমুর কাঁধে।
যে রাস্তায় সে হাঁটে, ঐ রাস্তার পাশে বাড়ির ছাদে কার্নিশ নেই কোনো। হিমু আসবে বলে নীল শাড়ি পরে যে ছাদের কার্নিশ ধরে রুপা সেজেগুজে দাঁড়ায়, প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও হিমু ঐ রাস্তায় কোনোদিন আসে না। হিমুর ঐ রাস্তায় আসা বারণ। হিমু তার ময়ূরাক্ষীর মতোই দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট আর গোপন।